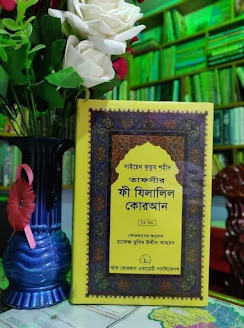|
| ঈদের নামায শেষে দোয়া পরিচালনা করছেন |
“রমযানের ঐ রোজার শেষ এলো খুশীর ঈদ” .........
ঈদ মুবারাক ...... ঈদ মুবারাক ...... ঈদ মুবারাক ...... আসসালাম।
ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে উৎসব। আজ ঈদ এসেছে সব ঘরে ঘরে, বিশ্ব মুসলিমের আজ আনন্দের দিন, সবচেয়ে বড় উৎসবের দিন। কিন্তু, বাংলাদেশ সহ সমগ্র বিশ্বের হাজারো পরিবারে আজ ঈদের আনন্দ নেই! বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি-হানাহানি-খুনাখুনি, যুলুম-নির্যাতন-সন্ত্রাস মানুষের সুখ-শান্তি কেড়ে নিয়েছে। বাংলাদেশের চারিদিকে, আমাদেরই আশেপাশে আজ কত পরিবারে বেদনার হাহাকার, কস্টের আহাজারি, অসহায়ের আর্তনাদ – ঈদের আনন্দ কি আছে তাদের ঘরে, অন্তরে? আমাদের পরিবারের অবস্থাও একই – আমাদের ঘরে, অন্তরে আজ বেদনার কান্না, চাপা কস্ট, কারণ আমাদের সবচেয়ে কাছের, সবচেয়ে প্রিয়, সর্বাধিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধার মানুষটি আমাদের মাঝে আজ নেই। তাই, আজকের দিনটা আমাদের জন্য আনন্দের না হয়ে বেদনার দিন, নিরানন্দের দিনে হয়েই থাকছে।
 |
| নামায শেষে পারিবারিক কবরস্থান যিয়ারত |
বাবাকে ছাড়া জীবনের এই প্রথম ঈদের দিন দেশে-বিদেশে আমাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ঈদের আসল আনন্দের দিন হতে পারেনি, হওয়া সম্ভব ছিলনা। যেই মানুষটা ছিল পরিবারের সকলের মধ্যমণি, বৃহত্তর পরিবারের সকলের অন্তরে বিশাল এক জায়গা নিয়ে এক বটবৃক্ষের মত, ছোট-বড় সকলের একান্ত আপন, তিনি আজ সবাইকে ফেলে রেখে তাঁর প্রিয় স্রস্টার সান্নিধ্যে; আর এদিকে আমাদের সবার মনের মাঝে বিরাজ করছে এক বিশাল শূন্যতা, ফাঁকা লাগছে সবকিছুই। উনার অবস্থান তো আর কাউকে দিয়ে পূরণ হবার নয়!
সেই ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, জেনেছি, উপভোগ করেছি - ঈদ মানে চরম উত্তেজনাকর এক অনুভূতি, অবাধে ‘বৈধ’ সকল আনন্দ করার লাইসেন্স। ঈদ-উল-ফিতরের (রমযানের ঈদ) চাঁদ দেখা থেকে পরদিন সারাদিন ঘুরে বেড়ানো এবং মজাদার সব খাবার খাওয়ার উত্তেজনা ও আনন্দ ছিল মাত্রাহীণ। “মহাকবি” নজরুলের (আমি তাঁকে “মহাকবি বলি”, “বিদ্রোহী কবি” বলিনা। আমি মনে করি নজরুলের প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে বেশী ছিল। নজরুলকে কেবলমাত্র “বিদ্রোহী”কবি আখ্যা দিয়ে সীমিত গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করে রেখে, রবীন্দ্রনাথকে “বিশ্বকবি”আখ্যা দিয়ে “ভগবান”এর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয়েছে সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে। এগুলো একশ্রেণীর বিকারগ্রস্থ লোকের মানসিক রোগের বহিঃপ্রকাশ। নজরুল ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন; নজরুলকে “বিদ্রোহী কবি” হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল তাঁকে খাটো করার উদ্দেশ্যে। এ নিয়ে কারো ভিন্নমত থাকতেই পারে। আমি বিতর্কে যেতে চাইনা; দয়া করে এ নিয়ে যুক্তিতর্ক শুরু করবেন না।) “রমযানের ঐ রোজার শেষ এলো খুশীর ঈদ” গানটি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের মনেই এক নাচন ধরিয়ে দেয়, দিচ্ছে গত ৭০/৮০ বছর হতে।
আমি একান্নবর্তী পরিবারে বড় হয়েছি। দাদা সহ বাবা-চাচা-ফুফু সকলেই পাশাপাশি থাকি। দাদার ছোট ভাই, আব্বাদের ছোট চাচাও পাশেই থাকেন। একেক বেলা ৫০ থেকে ৬০ জনের খাবার রান্না হতো। বাসায় ফল ও সব্জী বাগাণ ছাড়াও দাদার নাতি-নাতনীদের সব কিছু খাঁটি খাওয়ানোর ইচ্ছা থেকে বাসায় গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, কবুতর ইত্যাদি লালন-পালন করা হতো। শুনেছি সব মিলিয়ে কাজের লোকই ছিল ১৭ জন! তিন বিঘা জমির উপর পাশাপাশি সবার বাসা, কিন্তু একত্রে, দাদা-দাদু আর বড় বউ হিসেবে আমার মা এর তত্বাবধানে বাজার-রান্না-খাওয়া হতো; এক হুলুস্থুল অবস্থা। সবার বাসায় অবাধে যাতায়াতের জন্য ভিতর দিয়ে পকেট গেইট ছিল।
 |
| আমার সাথে কোলাকুলির পর হ্যান্ড শেইক |
এই পরিবেশে প্রাইমারী স্কুলে পড়ার সময় শাওয়ালের চাঁদ দেখার সে যে কি আনন্দ ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। চাঁদ দেখার পর সব কাজিনরা মিলে এ মাথা থেকে ও মাথা, এ বাড়ী থেকে সে বাড়ী দৌড়াদৌড়ি আর হৈ চৈ করার মধ্যেই ছিল আমাদের বিশাল আনন্দ! টিভি পুরা মহল্লা জুড়ে কেবল এক বাসায়; কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল, ফেইসবুক, ফাস্ট ফুড এসব শব্দ/ টার্ম তখন অনাবিষ্কৃত। তারপরও আমাদের সেই আনন্দের কোন সীমা ছিলনা। রান্নাঘরের আশেপাশে মা-চাচি-ফুফুদের ব্যস্ততা, কর্মতৎপরতা আর হাঁকডাক, পর দিনের জন্য নানান প্রস্তুতি; পূরুষরাও ব্যস্ত নানা কাজে। ঈদের দিন সক্কাল বেলা থেকেই গোসল আর নামাযের প্রস্তুতি চলতো সরবে। এরপর, দাদা উনার ছেলে ও নাতিদের নিয়ে নামাজে যেতেন রমনা থানার সামনের মসজিদে, কেননা তখনও দাদা আমাদের এই মসজিদটি নির্মাণ করেন নি। ঈদ-উল-ফিতর হলে নামাযে যাবার পূর্বে রাসূল (স.) এর সুন্নত অনুযায়ী সকলে নাস্তা সেরে নিতাম। যখন হাইস্কুলে উঠলাম, তখন গন্ডীটা একটু বড় হলো; পাড়ার বন্ধুদের সাথেও পাড়া জুড়ে হৈ হুল্লোড় করতাম তখন। সেই সময়ে পাড়ার মানুষরাও অনেকটা ‘পরিবার’ এর সদস্যের মতই ছিল। আমাদের এই ২০০ গজ লম্বা গলিতে তখন পরিবার ছিল মাত্র ৮/১০টা; এখন এই গলিতে ৩০০ এর মত পরিবার বাস করে! আমাদের হাই স্কুল জীবন শেষ হবার আগেই দাদা ইন্তেকাল করেন, চাচারা সব (একজন ডাক্তার, ২ জন ইঞ্জিনিয়ার) সরকারি চাকুরীর কারণে বিভিন্ন জায়গায় বদলী হয়ে যান, জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে সবাই পৃ্থক হয়ে যায়; ছোটবেলার সেই উত্তেজনায় অনেকটা ভাটা পরে যায়। আমাদের সেই দিনগুলো ছিল সত্যিই সোনালী দিন।
কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় ইংল্যান্ডে চলে গেলাম উচ্চ শিক্ষার জন্য। ঈদের আনন্দ, আমেজ, উত্তেজনা সব যেন হারিয়ে গেল, চলে গেল। ওখানে কেবল ঈদের ওয়াজিব নামাযটা আদায় করাই ছিল আমাদের ঈদ। সকালে নামাযে যেতাম কলেজের বইখাতা নিয়ে- নামায শেষ সোজা কলেজে ক্লাস করতে চলে যেতাম। বাংগালী/ বাংলাদেশী কমিউনিটি খুব ছোট ছিল। তাই এ বাসা ও বাসা বেড়ানোর তেমন কিছু ছিলনা। আমার আপন ছোট চাচা ছিলেন একই শহরে – রাতে উনার বাসায় খাওয়া হতো। সেই কয়টা বছর (১৯৭৫-১৯৭৮) ঈদ বলতে এই ই ছিল আমাদের দিনপঞ্জী।
 |
| নিজ হাতে ক্কোরবাণী দিচ্ছেন |
১৯৭৮ এর শেষে দেশে ফিরে ৮০ এর ফেব্রুয়ারিতে সেনাবাহিনীতে চলে গেলাম। ঈদের আনন্দ তখন ভিন্নমাত্রার; আনন্দ ও উত্তেজনা আর আগের মত থাকলোনা। একাডেমির ট্রেনিং এর দুই বছর অবশ্য ঈদে ছুটি পাওয়া যেত। তবে ছুটিতে বাড়ী এলেও নানা কারণে খুব বেশী আনন্দ উল্লাস করার মত মন মানসিকতা ছিলনা সেই বছরগুলোতে- মূলতঃ ট্রেনিংজনিত ক্লান্তির পর সময় পেলেই তখন বিশ্রাম নেয়া বা ঘুমানোটাই বেশী প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো। এছাড়া, বোধ করি ট্রেনিং এর ফলে কিছুটা মনস্তাত্বিক পরিবর্তনের ফলেও আর আগের মত সেই উত্তেজনা, উল্লাস বোধ করতাম না।
১৯৮১ এর ডিসেম্বরে কমিশণ পাবার পর হতে ২০০৯ পর্যন্ত যতগুলো ঈদ গেছে তার বেশীর ভাগই কাটিয়েছি ক্যান্টনমেন্টে। সেনানিবাসের ঈদ বিভিন্ন ‘ফরমাল’ আনুস্ঠানিকতায় পরিপূর্ণ থাকে- ছোটবেলার, কিশোর বয়সের ঈদ আর ফিরে পাওয়া যায়নি। ট্রুপ্স কমান্ডে সাধারণতঃ ছুটি পাওয়া যায় না; তবে যেই বছরগুলোতে স্টাফ অফিসার বা ইন্সট্রাক্টর হিসেবে চাকরী করেছি, সেই বছরগুলোতে ঈদে বেশ কয়েকবারই ছুটিতে এসে বাবা-মা এর সাথে ঈদ করার সুযোগ পেয়েছি। এর মধ্যে পাড়ায় আমার বয়সী ১২/ ১৩ জনের মধ্যে ২/১ জন ছাড়া বাকিরা সব হয় বিদেশে, না হয় অনত্র। যারা ছিল তাদেরও নিজস্ব একটা আলাদা গন্ডী (ব্যাবসা/ চাকুরীস্থল; শশুর বাড়ী ইত্যাদি) হয়ে গিয়েছিল; যার ফলে তারাও সেই বলয়ে ব্যস্ত দিন কাটাতো। সব মিলিয়ে, আর কখনো ছোটবেলার বা কিশোর বয়সের সেই “ঈদ” আর ফিরে পাইনি।
২০০৯’এ সামরিক বাহিনী থেকে “বরখাস্তের” পর আমার নতুন জীবন শুরু হলো ভিন্ন এক ধারায়। সেই বছর থেকে ২০১১ পর্যন্ত, এই তিন বছর বাবা-মা এর সাথে থেকেছি, ঈদ করতে পেরেছি। এই তিন বছর কিছুটা হলেও আবার ঈদের হারিয়ে যাওয়া আনন্দ ফিরে পাবার চেস্টা করেছি। কিন্তু, ২০১২’তে আব্বা গ্রেফতারের পর হতে আমাদের ঈদ আর কখনো “ঈদ” হয়নি! আর, এ বছরের ‘ঈদ’টা তো পুরো মাত্রায় ছিল বেদনার, রক্তক্ষরণের আর কস্টের! আম্মা সারাদিনই থেমে থেমে কান্নাকাটি করেছেন – ৬৫ বছরের জীবন সংগী ছাড়া প্রথম “ঈদ”; সহজেই অনুমেয়!
গত তিন বছরে আব্বার ৬টি ঈদ কেটেছে কারাগারে। এর আগে, ১৯৯২-৯৩’তে আরো ৪টা ঈদ তিনি কারাগারে কাটিয়েছিলেন। এরও অনেক আগে, আমার জন্মেরও পূর্বে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত তিনি ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে (!) তিনবার গ্রেফতার হয়েছিলেন। তবে যদ্দুর জেনেছি, তখন বন্দী অবস্থায় কোন ঈদ করতে হয়নি। আমার জন্মের পর, আমার ৫ বছর বয়সের সময় ১৯৬৪ সালে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইউব খানের সামরিক শাসনের সময় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আবার তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন। অবশ্য, সেই সময়কার কথা আমার তেমন মনে নেই, কেবল উনার মুক্তি পাওয়ার দিনের সামান্য কিছু স্মৃতি ছাড়া।
এবারে আব্বার গ্রেফতারের পর হতে ঈদের দিনগুলোতে নামায এর পরপরই সাক্ষাতের অনুমতির জন্য নাজিমুদ্দিন রোডে দৌড় দিতে হতো। অনুমতি পেলে সাক্ষাতে যাবার জন্য নানান প্রস্তুতি চলতে থাকতো যাবার আগ পর্যন্ত। এর মাঝে আত্মীয়-স্বজন এলে আবার সাক্ষাৎ ও সংগ দেয়াও লাগতো। ঈদ-উল-আযহা এলে তো ক্কোরবাণীর অতিরিক্ত দায়িত্ব চলে আসে। আমার সব ভাইয়েরা বিদেশে থাকায় তাঁদের ক্কোরবাণী দেশে আমাকেই সামাল দিতে হয়। ৩/৪টা গরু আর ২/৩টা ছাগল ক্কোরবাণী করে সব ভাগাভাগি করে বিতরণ করার ঝামেলা বেশ কস্টকর- তবুও করতেই হয়। আগে আব্বা সবগুলো নিজ হাতে জবেহ করতেন- পর্যায়ক্রমে গরু জবেহ এর দায়িত্বটা আমার উপর চলে আসে- আব্বা কেবল উনার নিজের নামে দেয়া ছাগল সহ অন্য ছাগলগুলো জবেহ করতেন। অবশ্য গত তিন বছর সেগুলোও আমাকেই জবেহ করতে হয়েছে।
যা হোক, আব্বার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি পাবার পর পরিবারের সকল সদস্যই সেদিন দেখা করতে যেতাম - আম্মা, আমি, আমার স্ত্রী এবং সন্তানরা। ঈদ ছাড়া অন্য সময় অবশ্য একসাথে সবাইকে অনুমতি দিত না, কেবল ৪ জনকে অনুমতি দিত; সময় মাত্র ৩০ মিনিট। ঈদের সাক্ষাতের ২/৩ দিন আগে থেকেই আমাদের প্রস্তুতি শুরু হতো উনার সাথে সাক্ষাতের। প্রস্তুতির মূল কাজ ছিল উনার জন্য রান্না করা খাবার তৈরীর আয়োজন। আয়োজন বললাম এই জন্য যে, ঘনিস্ঠ আত্মীয়-স্বজন সকলেই ঈদে আব্বার জন্য খাবার রান্না করে দিতে চাইতেন। তাই, ২/৩ দিন আগে থেকেই যারা যারা খাবার দিতে চায় তারা ফোন করে আলাপ পরামর্শ করতো, কে কি দিতে আগ্রহী তা জানিয়ে কনফার্ম করে নিত যেন ডুপ্লিকেশন না হয়। এটা সমন্বয়ের ঝামেলাটা অনেকটা ‘আয়োজন’ই হয়ে যেত কেননা সবাই এত বেশী আইটেম দিতে চাইতো অথচ আব্বা এত পরিমিত খেতেন যে তা নস্ট হয়ে যাবার আশংকাই বেশী ছিল। উনার ‘সেল’ এ কোন ফ্রিজ না থাকায় খাবার রেখে কয়েকদিন ধরে খাওয়া সম্ভব ছিলনা; তাই আইটেম এর সংখ্যা এবং টাইপ সমন্বয় না করে উপায় ছিলনা। আমরা যেই খাবার নিয়ে যেতাম, উনি তার সিকি ভাগও খেতেন না; বাকি সব কারারক্ষীদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। সারা জীবনই দেখেছি, কাউকে না দিয়ে উনি কখনো কিছুই খেতেন না। বাসার গাছের আম বা অন্য কোন ফল নিজ হাতে নিয়ে গিয়ে আশেপাশে উনার ভাইবোনদের বাসায় দিয়ে আসতেন। গাছে মাত্র ১টা আম হলে সেটাকেও কাটিয়ে টুকরা টুকরা করিয়ে কাজের ছেলেমেয়ে সবাইকে নিজ হাতে তুলে দিতেন খাবার জন্য, এরপর নিজে খেতেন। কি চমৎকার এক অনুকরণীয় আদর্শ তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্য! নবীজির (স.) এর সুন্নত অনুসরণে উনি ছিলেন আমার দেখা শ্রেস্ঠ নমুনা!
বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে যাওয়া একটু ঝামেলাপূর্ণ ছিল। বলা বাহুল্য, উনার জন্য দৈনিক বাসা থেকে তিন বেলা খাবার সরবরাহের ব্যাপারে আদালতের আদেশ থাকলেও আমরা তা দিতাম না। আমরা কেবল ঈদের দিন এবং নিয়মিত পাক্ষিক সাক্ষাতের দিন সাথে করে খাবার নিয়ে যেতাম। অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে যে, ‘কেন দিতাম না’? এ নিয়ে পরে অন্য সময় বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা রইল।
যা হোক, আনুমানিক বেলা ১টার মধ্যে বাসায় রান্না করা খাবার (তালিকা সহ) বাসা থেকে লোক দিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতাম। খাবার এবং তালিকা নিয়ে আমাদের লোক ডাক্তারের কাছে চলে যেত। ডাক্তার তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে (টিফিন বাটি খুলে, প্রত্যেকটি আইটেম দেখে, প্রয়োজনে মুখে দিয়ে টেস্ট করে) তালিকার নীচে লিখিতভাবে অনুমোদন করে স্বাক্ষর করে দিতেন। আমাদের প্রতিনিধি তখন ঐ খাবার সহ হাসপাতলেই অপেক্ষা করতো। আমরা যখন সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ে (নিয়মিত পাক্ষিক সাক্ষাতে বিকেল ৪টায় এবং ঈদের সাক্ষাতে বেলা ২টায়) হাসপাতালে যেতাম তখন আমি আমার হাতে খাবারটা নিয়ে নিতাম। প্রবেশের সময় প্রিজন সেল এর মূল ফটকে সকল গোয়েন্দা বাহিনীর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ডেপুটি জেলার নিজে তালিকা অনুযায়ী সব খাবার চেক করার পর আমি আমার হাতে করেই সকল রান্না করা খাবার আব্বার রুম পর্যন্ত নিয়ে যেতাম। অন্যান্য শুকনা খাবার এবং ব্যবহারের আইটেমগুলো গেইটেই কারা কতৃপক্ষ রেখে দিতে এবং পরে আব্বার নিকট পৌঁছানো হতো। প্রথম দিকে আমাকে হাতে করে রান্না করা খাবার নিয়ে যেতে দেয়ার ব্যাপারে কারা কর্তৃপক্ষ আপত্তি করলেও আমাকে নাছোরবান্দা দেখে কারা কতৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছে। আমি একজন প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং ওদের আইজি (প্রিজন) থেকেও সিনিয়র সেটা ওরা সবাই জানতো। তাই, দু’একজন ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই যথাযথ সন্মান দেখাতো ও সমীহ করতো এবং “স্যার” বলেই সম্বোধন করতো।
প্রিজন সেল এর সাইজ অনুমানিক ১৮০(১২X১৫) বর্গফুট। সাক্ষাতের সময় রুমের ভিতরে পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও আরো ৮/১০ জন লোক (কারা কর্তৃপক্ষ এবং সকল গোয়েন্দা বাহিনীর প্রতিনিধি) পুরা সময়টা দাঁড়িয়ে থাকতো; আমরা কি আলাপ করি তা খুব সিরিয়াসলি ওরা “নোট” করতো! পারিবারিক কথা ছাড়া আমাদের আর কোন কিছুই আলাপ হতোনা, কিন্তু তারপরও কি “নোট” করতো তা ভেবে আশ্চর্য্য হতাম! কয়েকবার ভেবেছি জিজ্ঞাসা করবো যে, “আমাদের পারিবারিক আলাপের ব্যাপারে কি নোট করছেন”? বিব্রতকর পরিস্থিতি হতে পারে ভেবে আর করিনি। প্রতিটি পরিবারের কিছু না কিছু পারিবারিক গোপণীয় বিষয় থাকে। কিন্তু সেগুলো গোপণে বলার মত কোন পরিবেশ সেখানে ছিলনা। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা এ বিষয়ে কখনো আপত্তি করিনি।
যা হোক, সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত এই ৩০ মিনিট আসলে খুবই অল্প সময়! সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করতে করতেই প্রায় ৮/১০ মিনিট লেগে যেত। এরপর উনাকে আমার সব ভাইদের ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের খবরাখবর সহ বৃহত্তর পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়দের গুরুত্মপূর্ণ কোন খবর (জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ইত্যাদি) থাকলে তা জানাতাম। এর বাইরেও আব্বা নাম ধরে ধরে অনেকের খবর নিতেন, এমন কি বাসার কাজের লোকদেরও খবর নিতেন। উনার প্রতিস্ঠিত মাদ্রাসার খোঁজ নিতেন এবং উনার কোন পরামর্শ থাকলে বলতেন, মসজিদের খবর নিতেন, উনার সহকর্মীদের ব্যাপারে জানতে চাইতেন, অন্য কাউকে কোন কিছু বলার মত থাকলে বলতেন, কাউকে সাহায্য করার থাকলে বলে দিতেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে আমার স্ত্রী আব্বাকে স্যুপ খাওয়াতো, মাঝে মাঝে হাল্কা নাশতা খাওয়াতো। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি স্যুপ ছাড়া আর কিছু খেতে চাইতেন না; অসময়ে কোন কিছু খাওয়া উনার স্বভাব বিরুদ্ধ – উনি বলতেন, “আমিই খুচরা খাই না”! এছাড়া, আমার স্ত্রী আব্বার হাত-পা এর নখ কেটে লোশন লাগিয়ে দিত। আমি দাঁড়ি-মোচ ছেঁটে দিতাম, গলায় (দাঁড়ির নীচে) শেভ করে দিতাম। এরই মধ্যে মূল ফটকে আমাদের রেখে আসা শুকনা খাবার আর ব্যবহারের জিনিষগুলো রুমে পৌঁছে দেয়া হতো; আমি লিস্ট ধরে সেগুলো আব্বাকে বুঝিয়ে দিতাম। এভাবেই সময়টা শেষ হয়ে যেত, উনাকে ভারাক্রান্ত মুখে রেখে আমরাও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে আসতাম। উনার ব্যবহার করা ময়লা কাপড় এবং অন্য কোন আইটেম উনি ফেরত দিতে চাইলে কারা কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে তা নিয়ে আসতাম।
গত ২০১৪ সালের ক্কোরবানীর ঈদ ছিল আব্বার জীবনের শেষ “ঈদ”, যদিও তা আসল “ঈদ” ছিলনা কোন অর্থেই। যদ্দুর মনে পরে, তারিখটি ছিল ৬ই অক্টোবর। সেদিন উনার যে করুণ অবস্থা দেখে এসেছিলাম, সেদিনই আমার মনে হয়েছিল, ‘উনার দিন বোধ হয় ফুরিয়ে আসছে’। কংকালসার দেহটা বিছানায় লেপ্টে ছিল, কথা বলতে পারছিলেন না, নিজের হাত-পা নাড়াবার ক্ষমতাও ছিলনা তখন উনার। কথা বলার চেস্টা করছিলেন, কিন্তু গলা দিয়ে কেবল ‘ফিসফিস’ শব্দ বের হচ্ছিল। মুখের কাছে কান লাগিয়ে অনেক কস্টে কিছু কিছু কথা বুঝা গেছে, অধিকাংশই বুঝা যায়নি। সেদিন উনার এই অবস্থা দেখে এসেই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে, অনেক চেস্টার করে দু’দিন পর উনাকে সিসিইউ’তে স্থানান্তর করা হয়েছিল। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় উনার অবস্থার ক্রমাবনতি হতে হতে ২৩শে অক্টোবর তিনি আমাদের ছেড়ে চিরতরে চলে যান।
উনার মুক্ত জীবনের শেষ বছরগুলোর ঈদে উনার কর্মকান্ড ছিল ছকে বাঁধা, যেন ক্লাসের রুটিন। ফযরের পর সামান্য কিছু বিশ্রাম নিয়ে উঠে গোসল করে নামাযের প্রস্তুতি নিয়ে নাস্তা সারতেন। তবে, ঈদ-উল-আযহা’র সময় নবীজির (স.) এর সুন্নত অনুযায়ী নিজ হাতে পশু জবেহ করে সেই পশুর গোশত রান্না হলে তারপর নাস্তা খেতেন। নামাযের আগে তিনি আনুমানিক ৩০ মিনিটের মত আলোচনা করতেন, আর নামাযের পর খুৎবা। উনার এই আলোচনা ও খুৎবা শুনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মুসল্লীরা আসতেন আমাদের মসজিদে। নামাযের পর খুৎবা ও দোয়া শেষ উনার সাথে কোলাকুলি করার জন্য লম্বা লাইন লেগে যেত। আমরা, পরিবারের সদস্যরা, কোলাকুলির সুযোগ পেতে অনেক সময় লেগে যেত, কখনো প্রায় আধা ঘন্টা! উনি যতক্ষন পারতেন দাঁড়িয়েই কোলাকুলি করতেন, এরপর চেয়ারে বসে বসে কোলাকুলি করতেন। কোলাকুলি শেষে মসজিদ সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থান যিয়ারত করতাম পরিবারের সকল পূরুষ সদস্য একত্রে মিলে। এই কবরস্থানে আমার দাদা-দাদু, এক চাচা (এখন আব্বারা ৪ ভাই; আব্বা জেলে থাকাকালীন ২০১৩ এর জানুয়ারিতে এক চাচা ইন্তেকাল করেন। তিনি তখন প্যারোল এ মুক্তি না পাওয়ায় জানাযা বা দাফনে অংশ নিতে পারেন নি। আরেক চাচা ইন্তেকাল করেন আব্বার ইন্তেকালের পর, জানুয়ারি ২০১৫’তে), এক ফুফু (আব্বা কারাবন্দী থাকাকালীন ডিসেম্বর ২০১২’তে ইন্তেকাল করেন), দুই চাচী, এক ফুফা এবং আমার বড় ভাবী’র কবর রয়েছে। এছাড়া, পেছনের দিকে (মসজিদের পূর্ব দিকের পায়ে চলা পথ দিয়ে সোজা উত্তরে শেষ প্রান্তে) আরো একটা পারিবারিক কবরস্থান রয়েছে আমাদের- সেখানে কবর হয়েছে আমার বড় ফুফু ও নানীর। ওটাও সকলে মিলে একত্রে যিয়ারত করতাম। যিয়ারত শেষে, সবাই মিলে পাশেই আব্বার ছোট চাচী (আব্বার জীবিত একমাত্র মূরুব্বী ছিলেন। তিনিও আব্বা কারাবন্দী থাকাকালীন ইন্তেকাল করেছেন।) থাকেন, উনার সাথে সাক্ষাৎ করতাম। এরপর আব্বা বাসায় চলে আসতেন আর আমরা বাকিরা অন্যান্য মূরুব্বীদের সাথে সাক্ষাৎ করে যার যার বাসায় ফিরতাম।
সারাদিন আব্বার সাথে সাক্ষাতের জন্য আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ আসতেন। তবে, যে কোন অবস্থায়ই আব্বা নিজ রুটিন যথারীতি অনুসরন করতেন; অত্যন্ত সুশৃংখল জীবনযাপনেও তিনি ছিলেন এক উৎকৃস্ট নমুনা। যোহরের নামাযের আধা ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত সাক্ষাৎ করে তিনি নামাযের প্রস্তুতি নিয়ে মসজিদে চলে যেতেন। অধিকাংশ দিন বেশীর ভাগ ওয়াক্তের নামাযে তিনিই প্রথম মূসল্লী হিসেবে মসজিদে প্রবেশ করতেন। যোহর শেষে বাসায় ফিরে খাবার খেয়ে বিশ্রাম নিতেন। অন্যান্য সময় বাসায় উনার নিজস্ব বেডরুমে বিশ্রাম নিলেও ঈদের দিন যেহেতু সারাদিন মেহমান আসতে থাকতো, তাই মেহমানদের বেড়ানো যেন বাধাগ্রস্থ না হয় এবং একই সাথে উনার বিশ্রামেরও যেন কোন সমস্যা না হয় সেই লক্ষ্যে বাসার সাথেই যে উনার চেম্বার আছে সেখানে একটি বিছিনা রাখা ছিল, উনি সেটাতেই বিশ্রাম নিতেন। আসরের সময় যথারীতি নামাযে সেরে, এর পর হতে রাতের খাবারের পূর্ব পর্যন্ত (মাগরিব ও এশা সময়মত মসজিদে যেয়ে পরতেন) আবার সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সাথে দেখা করতেন। রাত ১০টায় রাতের খাবার সেরে সাড়ে ১০টায় খবর দেখতেন; ১১টা নাগাদ বিছানায় চলে যেতেন। যতক্ষন পর্যন্ত ঘুম না আসতো ততক্ষন টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়তেন; ঘুম এলে লাইট নিভিয়ে ঘুমিয়ে পরতেন। উনার এই রুটিন এর কোন হেরফের হতোনা কখনো; এমন কি গ্রেফতারের আগের রাতেও (১০ই জানুয়ারি ২০১২) না।
আজকের এই ঈদের দিনে আমাদের মনে কোন আনন্দ নেই, উল্লাস নেই, খুশী বা উৎসবের কোন আমেজ নেই। নিছক আনুস্ঠানিকতা করার জন্য যা যা করা দরকার তা-ই করেছি, দূঃখ ও ভারাক্রান্ত বেদনাবিধুর মনে; বার বার মনে পরেছে বাবার কথা, তাঁর রেখে যাওয়া হাজারো স্মৃতি। আমিই জানি, এই অবস্থা কেবল আমাদের পরিবারেই না, এমন অবস্থা এখন এদেশের হাজারো পরিবারের। কাতর হয়ে মহান স্রস্টার কাছে বিনীতভাবে দোয়া করি যেন তিনি সকল মযলুমের মনের ব্যাথা দূর করার জন্য যা প্রয়োজন তা “কুন” বলে হবার ব্যবস্থা করে প্রতিটি পরিবারে কিছুটা হলেও সুখ ও শান্তি আনার ব্যবস্থা করে দেন, আমীন!
তারিখঃ ১৮ই জুলাই ২০১৫